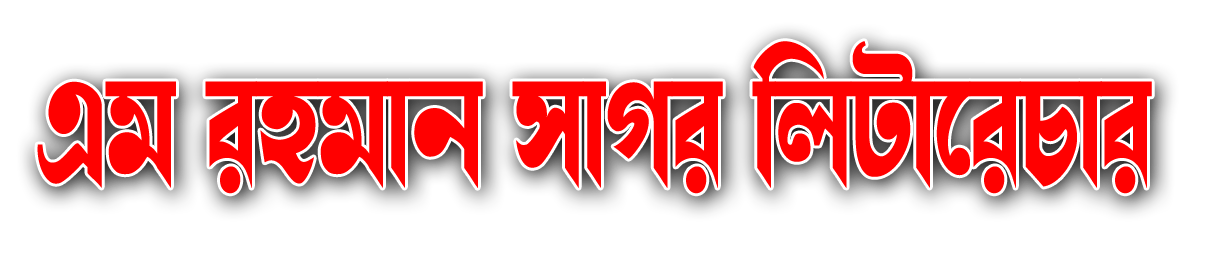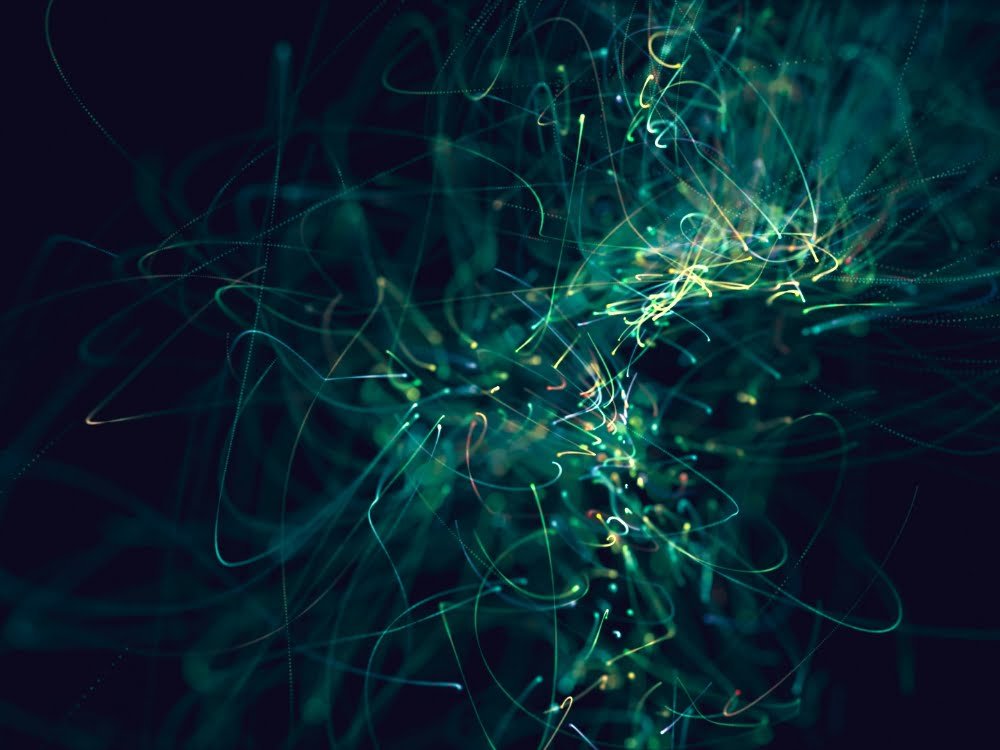দূর—বহুদূর— পরিমাপে এক মনের দূর, পরিমাণে যোজন যোজন দূর; অথচ মনের জানালা খুললেই সে দূরত্ব হয়ে যায় চোখের দূরত্ব। ওতোটুকু দূরত্ব পেরোলেই দেখা মিলে দূরভূমির—সে দূরভূমিতে শস্য ক্ষেত, সে ক্ষেতে কাকতাড়–য়া। কাকতাড়–য়ার আত্নজের মনটা বিষণ্ণ, মুখে কষ্টের অভিব্যক্তি— কত ধারদেনা আর কষ্ট করেই না ফসল ফলাতে হয়েছে। আর কটা দিন গেলেই ধান কাটতে পারবে। অথচ এ ক’দিনেই বোধ হয় ক্ষেতের অবস্থা আধাআধি করে ছাড়বে—ইঁদুর। তাই, ইঁদুরের আস্তানা খঁুজে খঁুজে সুলতান কাকতাড়–য়া গাড়ার চেষ্টা করছে। মুক্ত বাতাস মাখা থৈ থৈ রৌদ্দুর দুলছে—সবুজ আর সোনালি বুনন মাঠের আকাশে। চাপা একটা আওয়াজ বিরাজ করছে মাঠের চারদিকে— পাখির কিচিরমিচির, গরুর হাম্বা, রাখালের বাশি, কৃষকের ধোয়া গানের মিশেল। মাঠের কারিগড় যারা— আদিপান্ত চিনি চাষা বলে যাদের, তাদেরই এক জন এই সুলতান মিয়া। বয়স চল্লিশ ছুঁয় ছুঁয়, পৈত্রিক সূত্রে বিঘা চারেক জমির মালিক, বৃদ্ধ বাবা—মা, দুই সন্তান আর স্ত্রীকে নিয়ে ছোট একটা সংসার। কৃষি কাজ করে এ ছোট সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয় সুলতানকে। তবু এ কাজই তার শেষ ভরসার স্থল—কৃষির এদিক ওদিক হলেই যে টলমলিয়ে উঠে তার সংসার জীবন।
দিগন্ত জোড়া মাঠকে দু’ফালি করা রাস্তা ধরে— সাংবাদিকের মটর সাইকেল ছুটে আসে এদিকে। ভো ভো আওয়াজ তুলে সুলতানের জমির কাছে এসে থামে, তারপর ডাকে সুলতানকে— ‘কি মিয়া মাঠের সুলতান, ফসলে ইঁদুর লাগছে নি?’ সুলতান মুখ ঘুরিয়ে জবাব দেয়— ‘হ সাংবাদিক ভাই, এঁন্দুর দেখছি বড় বেহামি শুরু করেছে।’ সাংবাদিক মটর সাইকেল থেকে নামতে নামতে বলে, ‘ভাল করে ইঁদুর তাড়াও, এবার ধানের ভাল দাম পাবা—মিয়া।’ সুলতানের কানে কথাটি লাগে বটে, কিন্তু গুরত্ব পায় না, কাকতাড়–য়ার পোশাক ঠিক করতে করতে অবজ্ঞায় জানতে চায়—
—কেমনেরে ভাই?
—সরকার ধানের দাম নির্ধারণ করছে মণ প্রতি ৮০০ টাকা। বুজছো মিয়া— সাংবাদিক জানায়।
—তয়, হামরা কি সে দাম পামু ভাই— হতাশা ঝরে পড়ে সুলতানের কন্ঠে।
—কেন, পাবা না?
—বাজারে কত এঁন্দুর আছে না ভাই?—বলতে বলতে কাকতাড়–য়া ভাল করে গেড়ে নেয়, সুলতান।
কাঁধের ব্যাগ বাম পাশ থেকে ডান পাশে রাখতে রাখতে সাংবাদিক মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি প্রকাশ করে বলে, ‘মন্দ কও নাই—সুলতান। তো, বাজারের ইঁদুর তাড়াবে কোন কাকতাড়–যায়?’
সুলতান ক্ষেত থেকে রাস্তার দিকে উঠে আসে, আসতে আসতে বলে,‘ক্য ভাই, তোমরা আছো না?’
স্কুল ফেরত এক দল বালক হৈ—হুল্লর করতে করতে সাইকেল চালিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে চলে যায়। সুলতান এসে সাংবাদিকের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সাংবাদিক সুলতানের কাঁধে হাত রেখে বলে, ‘ভালই তো বলছো ভাই, তো বলো—তোমাদের জন্য কি করতে পারি?’
সুলতান কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলা শুরু করে— ‘এই যে তুমি আসেই কলে, সরকার ধানের দাম ঠিক করেছে ৮০০ টাকা মণ। কিন্তু সেই ধান—চাল কি হামাকেরে কাছ থেকে কিনবি? কিনবার লয়; কিনবি তো চাতাল মালিকদের কাছ থেকে। তয়, ওকেরে কাছ থেকেই যদি কিনবি, তাহালে হামাকেরে খরচের হিসেব ধরে দাম ঠিক করে লাভ কি? ওরা তো আর হামাকেরে কাছ থেকে ৮০০ টাকায় কিনবার লয়। ওরা হামাকেরে কাছ থেকে কম দামে কিনে, লাভ করে সরকারকে দিবে—নাকি? তাও কি হামাকেরে প্রয়োজনের সময় কিনবি, কিনবি তো ফসল উঠার পর, যখন হামাকেরে ঘরে ধান থাকবার লয়।
—হুঁ, তা তো বটে। সাংবাদিক মাথা ঝাঁকায়।
—হামাকেরে কাছ থেকে যদি সরাসরি না কিনে, তাহালে হামাকেরে উৎপাদন খরচ হিসেব করে দাম ঠিক করে লাভ কি? সুলতান তপ্ত কন্ঠে জিজ্ঞেস করে।
সাংবাদিক ঠোঁট ভেল্টিয়ে জবাব দেয়, ‘সেই তো কথারে ভাই।’
—সে কথাই তুমি ল্যাখো, তাহালেই তো হামাকেরে উপকার হয়। অনুরোধের সুর ঝরে পড়ে এবার সুলতানের কন্ঠে।
—কিন্তু, কৃষক—ধান—ফসল এগুলো তো অতো গুরত্ব পায় না পাঠকের কাছে। তাই পত্রিকায় তোমাদের সংবাদের গুরত্বও কম। আপসেট গলায় নিজেদের অপারগতার কথা জানায় সাংবাদিক।
সুলতান একটু তেতিয়ে উঠে, মুখে এক রাশ হতাশা ফুটিয়ে বলে, ‘তাহালে মাঠের কাকতাড়–য়া আর মানুষের মধ্যে তফাত হলো কুনটি?’
সাংবাদিক মটরসাইকেলে উঠে বসতে বসতে বলে ‘দ্যাখি, তোমাদের জন্য কিছু লেখা যায় কিনা’ বলে মটরসাইকেল ছেড়ে দেয়। সাংবাদিকের ছুটে চলে যাওয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয় কিছুক্ষণ, চোখ জোড়া থেকে আকুতি ঠিকরে পড়ে—তাঁর, সে আকুতিকে পিছনে ফেলে সাংবাদিকের মটর সাইকেল দৃষ্টি সীমানার বাহিরে চলে যায়। সে দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সুলতান বলে, ‘গুরত্ব’… বিড়বিড় করে আবারো বলে ‘হায়রে গুরুত্ব’…মুখে বেদনার ছাফ স্পষ্ট, ভিতরটাও বেদনায় ডুকরে উঠে— হায়! এতো কষ্ট করে আমরা ফসল ফলায় বলেই না, দেশের মানুষ খেতে পারে; অথচ আমাদের কিনা গুরত্বই নেই কোথাও?
প্রকৃত ঘটনা হলো, বাংলার কৃষকদের নন্যতম যে অধিকার ও সন্মান পাওয়ার কথা; তা তারা কোথাও পায় না। এই ধরুন, সরকারি পর্যায়ে ধান—চাল ক্রয়ের ব্যপারটি। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে উৎপাদন করে কৃষক, সেটা সরকারের কাছে বেশী দামে বিক্রি করার সুযোগ পায় অন্যরা। অথচ মূল্য নির্ধারণ করা হয়, কৃষকের উৎপাদন খরচ হিসাব করে। এটা কি তামাশা নয় কৃষকের সাথে? অনেক আলাপ—আলোচনার পর ঠিক হয়, কৃষক পর্যায় হতেও সরাসরি কিছু ধান ক্রয় করা হবে। কিন্তু, এবারের তামাশাটা ঠিক জন্মদাতা পিতাকে অস্কীকার করার মতো— কৃষক নাকি ঠিকঠাক ধানের আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, অথ্যাৎ ধান শুকাতে পারে না— এমন অভিযোগ তোলা হয়। আরে ভাই, হাজার বছর ধরে যাদের হাতে সুরক্ষিত রইলো কৃষি, যাদের প্রশস্থ কাঁধে ভর করে আজকের খাদ্যনিরাপত্তা, তারাই যদি কৃষি কাজ না জানে: তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলতেই হয়—এমন অভিযোগ নিশ্চয় গুরত্বের গুরত্বই হারিয়ে দেয়, না কি ?
মাঠ ভর্তি ফসল বলেই কি না, চারদিকের খরতাপের রোদকেও থৈ থৈ রোদ্দুর মনে হচ্ছে। অথচ যেদিন শূন্য মাঠের ফাঁকা জমিন চাষতে হয়েছিল, সেদিনের রোদকে ঠিকই খাঁ খাঁ রোদ্দুর মনে হয়েছিল। সে খাঁ খাঁ রোদেই পিট পুড়ে, হালের গরুর সাথে চিল্লায়ে ‘হুট..হুট..বায়ে যা..বায়ে যা..বারাবল..বারাবল..ডানে..ডানে..’ এরকম বাম—ডান করে জমি চাষতে হয়েছে। হাতের নিপুন দক্ষতায় কাঠের লাঙ্গলে জমিন দু’ফালি হয়েছে। দু’ফালি থেকে চো’ফালি তারপর ছ’ফালি। সেই ফালাফালিতেও ডিগবাজি খেয়েছিল সুলতানের স্বপ্ন:
সুলতান হাল ছেড়ে দিয়ে চাষ হওয়া জমির দিকে হাসি মুখে তাকায়। বুকের ভিতর ধক করে উঠে ‘বীজ, সার, তেল কিনার টাকা পাবে কোথায়—সে?’ তখন, হাসি মুখ বেদনায় ভরে উঠে মুহুত্বে, তবু ভিতরে শক্তির সঞ্চয় করে বিড়বিড় করে আওরায়— ‘হবে হেনি একটা ব্যবস্থা’, বলে লাঙ্গল জোয়াল কাঁধে তুলে বলদ জোড়া নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। হাঁটতে হাঁটতে চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খায়— টাকার ব্যবস্থা কোথায় থেকে হবে তাঁর। আসলে সে হাঁটে না, সাঁতরায় চিন্তার সমুদ্রে, কিন্তু সে সাঁতরানোয় কোন কূলকিনারার দেখা পায় না। অতুল সমুদ্রে হারিয়ে বারবার শত বঞ্চনার কথা মনে পড়ে: গেল বারই কিনা ব্যাংকে বার কয়েক ঘুরে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ম্যানেজার পর্যন্ত অতি কষ্টে পেঁৗছালেও কেবল ছালাম টুকুই বিনিময় হয়েছে আর ম্যানেজারের জিজ্ঞেসা, ‘কি ভাই?’
—স্যার, লোনের জন্য কথা কয়তাম; সুলতানের নীচু কন্ঠে উত্তর ছিল।
—কি করেন ?
—কৃষি কাজ করি।
—ও আচ্ছা.., আমরা তো এখন ব্যস্থ, পরে অন্যদিন আসেন।
সুলতান মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসতেছিল, ম্যানেজার তাঁর দিক যে ভাবে বিরক্ত নিয়ে তাকিয়ে ছিল। আজও সে তাকানো সুলতানকে ছোবল মারতে চায়; যে কারণে, সুলতান ঐ দিকে পা মারতে সাহস পায় না আর।
তাই, বাজারের বীজ—সার—তেলের দোকানে সুলতান ধরনা ধরে। এবার আর ঝামেলা করবে না, এমন অজ¯্র তেল মারা কথায় দোকানির মন গলাতে চেষ্টা করে। দোকানি ঝাঝালো কন্ঠে দু ডন্ড বকে নেয় আগে— ‘মিয়ারা.. বারবার তো একই কথা কও, তয় টাকা দেওয়ার বেলায় তো খালি ঘুরাও।’
—এবার ঝামেলা করুম না ভাই; আত্নসমর্পণের ভঙ্গিতে মিনমিনিয়ে বলে সুলতান।
—ঠিকঠাক মনে থাকে যেন, বলে দোকানি বীজ—সার—তেল মেপে দেয়। সুলতানের মুখখানা চাদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সাইকেলে সব কিছু বেধে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়। মুখে গুনগুনিয়ে গান। অথচ প্যাডেল ঘুরছে ক্যরক্যর শব্দে, তাতে অতি কষ্টে পা চালায় সুলতান। সাইকেলের চাকা ঘোরে বটে, তবে সুলতানের শরীর ঘেমে একাকার, মুখ মন্ডল ঘর্মাক্ত, তবু মুখে গুনগুনিয়ে গান, এই না হলে— বাংলার চিরঞ্জীব যোদ্ধা?
তারপর এসে সুলতান মজে যায় কাদাজলের কাজে। নোংরা কাদাজলে দু’মুঠো বীজ ছড়িয়ে ভুবন জয়ের হাসি খেলে যায় সুলতানের মুখে, হুট করে ক’দিন পরেই সে বীজ থেকে দুটি সবুজ কুড়ি ফিঁক করে হেসে উঠে। মুক্ত বাতাস আর তেজ মাখা রোদে সবুজ কুড়ি জোড়া পাতা—পল্ববে দুলিয়ে উঠে। দুলিয়ে উঠে সুলতানের মন— তাই, কখনো ঢালে পানি, কখনো দেয় সার, কখনো দেয় দু’হাতে নিরানি। এতো পরিচর্যা থাকলে কে আর দমে থাকে বলেন, সবুজ কুড়ি গুলো হয়ে উঠে তাই সবুজের লন। বাতাস খেলে যায় সে সবুজের বুক চিরিয়ে, পাখিরা ডানা মেলে উড়ে, ব্যাঙেরা সবুজের লনে বসে ঘঁ্যাঙোর ঘঁ্যাঙ গান ধরে, চোখ জুড়ে যায় তখন সে সবুজে তাকিয়ে: এ যে কেবল সবুজরই লন নয়—স্বপ্নেরও বাগিচা বটে। স্বপ্নের বাগিচা—সবুজের সে লন কোন একদিন আড়মোড়া ভেঙ্গে ছড়াতে থাকে সোনালি আভা। যে আভার আঁধারে হাবুডুবু খায় উন্নয়নতত্ত্ব, অর্থনীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব। তবুও আলোচনার সহায়ক বিষয় হিসাবে এ বিষয়টি কখনও গুরত্বের পর্যায়ে পড়ে না। নান্দনিকতার ছায়াও পড়ে না এদের উপর। তাদের কাছে হয়তো এসব প্রসঙ্গ বিশেষ জরুরিও নয়। খুব সাদা—সিধে ভাবে তাকালেই দেখা যায়—কত নিপুন আর নিষ্ঠার সাথে নিজেদের কাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ তাঁরা। সোনালি আভা ছড়ানো সে মাঠে সুলতানেরা ব্যস্ত হয়ে উঠে, মুঠো মুঠো সোনালি ধান নুয়ে পড়ে তাদের হাতে; মুখে তখন বাধ ভাঙ্গা গান..[ এই তো বৈশাখো মাসে কৃষাণো কাটে ধান/নারীরও যৌবন বাড়ে, লাউ—কুমড়োর লাহান/লাউ নয়—কুমড়ো নয় জাঙ্গিলায় রাখিবে/নারী হয়ে এই রুপ—যৌবন রাখবে কতদিনে—কুনক্ষানে…], হুকার সারি জমির আইলে রাখা—সাথে আগুনের বুন্দি; বুন্দি হতে মিহি মিহি সাদা ধেঁায়া উড়ে। জমির আইল ধরে সুলতানেরা সারিবদ্ধ ভাবে ধান কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরে। কৃষাণী বধুকে উঠানে ধান নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করতে হয়। উঠান জুড়ে ধান ছড়ানো থাকে। সে ধানেতে পা দিয়ে পিট উল্টে দেয় কৃষাণী বধু, তখন তার পায়ের নূপুরের তালে ধানও যেন উঠে নেচে। এক হাট বারে সে ধান বাজারে নেয় সুলতান। তাতে, কৃষাণী বধূর হৃদয় মুচরে উঠে; সুলতানের হৃদয়ও হয়তো। তবুও আহত হৃদয়ে বাজারে ছোটে সুলতান। দোকানের বাকি শোধ না করলে, ফি বছর যে ফসলই করা হবে না।
হাটে প্রচুর লোকসমাগম, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সুলতানকে ধান বিক্রি করতে দেখা যায়। টাকা গণে নিতে নিতে সুলতানের চোখে ভাসে নানান স্বপ্ন— বউ’র জন্য নতুন শাড়ি, নাকের লোলক, হাতের চুড়ি, বাচ্চাদের জামা—কাপড়, ভালোমন্দ একটু খাবার…কিন্তু চিন্তা মোচড় দিয়ে উঠে মাথায়— তাহালে বাজারের বাকি শোধ হবে কিসে? টাকা গণার পর থমকে যায় সুলতানের স্বপ্ন— ধান বিক্রির টাকায় যে গঞ্জের বকেয়া—ই শোধ হতে চায় না। সুলতান ভারাক্রান্ত মনে মাথা নিচু করে হাটের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। দোকানে দোকানে গিয়ে পাওনাদারদের বকেয়া পরিশোধ করে; তারপর রিক্ত—সিক্ত হাতে বাড়ির পথ ধরে—সুলতান। শূন্য বস্তা কাঁধে রাস্তার পাশ ঘেষে হাঁটতে থাকে। হাট থেকে গঞ্জের দিকে ছুটে চলা ধান বোঝায় ট্রাক সুলতানকে অতিক্রম করে চলে যায়। সুলতান সে দিকে হতাশার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়। সচল পথ যেন অচল হয়ে উঠে তার সামনে: স্থির হয়ে যায় দৃষ্টির সীমানা, হাত—পা সামনে পিছনে নড়ে না এক ইঞ্চিও— ঠায় দাঁড়ানো মাঠের কাকতাড়–য়া মনে হয় তখন সুলতানকে। আসলে সুলতানেরা তো কাকতাড়–যায়, তাদের ঘাম ঝরা কষ্টের উৎপাদিত ফসলের লাভ যে অন্যের গর্তেয় যায়।